বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি আর বজ্রকঠিন চরিত্রের কল্পকথাগুলি একটু একটু করে ধুলো হয়ে উবে যাচ্ছে অনেকদিন হল। এখন তর্কটা এসে দাঁড়িয়েছে তিনি আদৌ এদেশের – দেশের মানুষের – জন্য শুভ কিছু, কল্যাণকর কিছু করে – বা অন্তত শুরু করে – যেতে পেরেছিলেন কি? নাকি স্রেফ ব্রিটিশ প্রভুদের ইশারায়, অঙ্গুলিহেলনেই বাঁধা ছিল তাঁর কার্যপরম্পরা? ঘুলিয়ে ওঠা কাদাজল সামান্য স্বচ্ছ করার প্রচেষ্টায় অশোক মুখোপাধ্যায়। এটি পঞ্চম পর্ব। প্রথম , দ্বিতীয়,তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব ক্রমান্বয়ে এখান থেকে পড়া যাবে – লিংক এক, দুই , তিন, চার। আগে প্রকাশিত পর্বগুলি ফেসবুকে লিখিত নিবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ ছিল। এ পর্ব থেকে সবটাই লেখকের নতুন সংযোজন।
[৯]
আরও কত অদ্ভুত সব অভিযোগ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। তিনি এত স্ত্রীশিক্ষার কথা বললেন, মেয়েদের জন্য কত স্কুল খুললেন, অথচ তাঁর নিজের স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাননি। দান ধ্যানের কথা বলছেন? সে পাঠ্যপুস্তক লিখে নিজের প্রেসে ছাপিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে সমস্ত স্কুলে সেই সব বই অবশ্যপাঠ্য করে দিয়ে বছরের পর বছর কত টাকা কামিয়েছেন জানেন? পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, বুঝলেন? হ্যাঁ। সেই জন্যই তো সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজের দরজা গোরা সৈন্যদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একেবারে সুবিধাবাদী লোক মশাই। সে আপনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে যতই ইনিয়ে বিনিয়ে গলা ফুলিয়ে বলুন, ইনিও আসলে একেবারে আমাদের মতোই। খাঁটি বাঙালি।
আমাদের তরফে কিছু কথা তাহলে বলতেই হয়। প্রথমেই বলি, বিদ্যাসাগর যদি সত্যিই তাঁর নিজের স্ত্রীকেও শিক্ষার দোরগোড়ায় নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে তো ভালোই হত। তবে আমরা কিন্তু জানি না, বিদ্যাসাগর চাননি বলে এমনটা ঘটেছে, নাকি, দীনমণি দেবী নিজেই ঘরকন্নার বাইরে এসে আর কিছু করতে চাননি।
দ্বিতীয়ত, এই প্রশ্নটা আমরা এখনকার দিনেও কজন সমাধান করতে পেরেছি যে মুখে যে আদর্শের কথা বলছি, পরিবারেও তা প্রয়োগ করতে চাই এবং করেছি? আমার পরিচিত নারী পুরুষ মিলিয়ে শতকরা ৯৮.৭৩ জন, যাঁরা{ক্যালেন্ডারে ২১ ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ আর ১৯ মে এসে গেলেই} ফেসবুকে বাংলা ভাষার পক্ষে গলা ফাটিয়ে আহাজারি করেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁরাই আবার নিজেদের সন্তানকে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন। কত জন যুক্তিবাদী বামপন্থী মার্ক্সবাদী বলে পরিচিত জনেরা তাঁদের বাড়িতে পুজো নামাজের প্রকোপ বন্ধ করতে পেরেছেন? শতকরা কজন হাতে অত্যন্ত দামি স্মার্ত ফোন নিয়ে আঙুলে রুবি নীলা বৈদুর্যমণি শোভিত আংটি বা ছেলের গলায় মন্ত্রপূত মাদুলি, মেয়ের বগলে কোনো পবিত্র থানের লাল সুতো, ইত্যাদি ব্যবহার করেন না? ভয়ে ভয়ে কাউকে এসব নিয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে কেউ মা এবং/অথবা স্বামী/বউয়ের ঘাড়ে দায় চাপান, কেউ বলেন পরিবারের চাহিদা, পরিস্থিতির চাপ, ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিদ্যাসাগরের বেলায় অবশ্য এগুলোর কোনোটাই আমাদের আর মনে থাকে না। বর্তমান যুব প্রজন্মের ভাষায় সবই কেমন যেন“চাপলেস” হয়ে যায়!
তৃতীয়ত, সাধারণ গড়পরতা মানুষদের কথা না হয় ছেড়েই দিন। আমরা ইউরোপ থেকে শুরু করে আমাদের দেশের রেনেশাঁস পর্যন্ত যখন বিবেচনা করি, কজন মনীষীকে পাই, যাঁরা তাঁদের স্ত্রীকেও, সন্তানদেরও, নিজ নিজ আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন? দুচারটে উদাহরণ খুঁজে বের করুন দেখি আগে! হ্যাঁ, এটা একটা সীমাবদ্ধতা, মানব জাতির শ্রেণি বিভক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ ঐতিহ্যের জের হিসাবেই যা সর্বত্র চলে এসেছে। কার্ল মার্ক্সের মতো সচেতন ভাবে কেউ কেউ হয়ত পরবর্তীকালে ভাঙতেও চেয়েছেন। কিন্তু কজন পেরেছেন? অর্থাৎ, আমার বক্তব্য হল, এটা আলাদা করে বিদ্যাসাগরের কোনো ত্রুটি নয়, কোনো একজন বা দুজনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয়; এ একটা সমাজ ইতিহাসের সমস্যা, যাকে এখনও মানব জাতি সমাধান করে উঠতে পারেনি। অভিযোগটা তোলার আগে পাঁচ মিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত মনে মনে কল্পনা করে নিজেদের চারপাশটা একবার দেখে নিলেই সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝা যেত। কিন্তু নাঃ, আমাদের একমাত্র দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিযোগ করা।
এবং এর জন্য আর একটা কাজও এনাদের করতে হয়। তা হল, এই সব অভিযোগের সারবত্তা স্থাপনে ভুলে থাকা যে “আসামী” বিদ্যাসাগরই আবার নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে যারপরনাই খুশি হন, “তোমার জননী দেবী কিংবা মাতামহী মহাশয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন” বলে তাকে নিরস্ত করেননি। এমনকি, সেই পুত্র যখন পরে আবার বিবাহিত স্ত্রীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়ে পড়ল, তিনি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। আদর্শ থেকে বিচ্যুতির জন্য এরকম কঠোর অবস্থানের ঘটনা শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবীতেই আর কটা আছে সন্দেহ।
বিদ্যাসাগরকে সুপারম্যান না ভাবলে, তাঁকেও রক্তমাংসে গড়া ইতিহাসের বিশেষ দেশ ও কালের মূর্ত মানব বলে ভাবতে পারলে তবেই এই সব প্রশ্নে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। ফুটোস্কোপ দিয়ে দেখলে পাওয়া যাবে না। আর আমার এও মনে হয়, আমরা প্রতিদিন যে অসংখ্য আপস করতে থাকি জীবনের চলার পথে, সেখানে এই অদ্বৈত আদর্শলগ্নতার দৃষ্টান্তটির অস্তিত্ব যেন আমাদের গায়ে নিভৃতে নিঃশব্দে সুচ ফোটায়! তখন এক তীব্র প্রক্ষোভের আপ্লবে বিদ্যাসাগরকেও আমাদের পংক্তিতে টেনে নামানোর প্রয়োজন পড়ে।
দ্বিতীয় কিস্সা: পাঠ্যপুস্তক বাণিজ্য।
এও এক আজব প্রশ্ন। সবার আগে তো জেনে নিতে হবে, সেকালে কোন কোন বিষয়ে কটা পাঠ্যপুস্তক ছিল। বিদ্যাসাগর যে বইগুলো লিখেছিলেন, সেই সব বিষয়ে তার চাইতেও ভালো ভালো পাঠ্যপুস্তক কে কে লিখেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা সেই যুগের একটা বড় কাজ, বড় দায়িত্ব ছিল। ১৮৪৩ সালে অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় লিখছেন “ভূগোল”, তারপর ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখলেন “প্রাকৃত ভূগোল”। বই কোথায়? ছাত্ররা পড়বে কী?
আমাদের প্রজন্মের অনেকেই হয়ত মনে করতে পারবেন, ১৯৫০-৬০-এর দশকগুলোতে স্কুলে স্কুলে কেশব চন্দ্র নাগের পাটিগণিত, কে পি বসুর বীজগণিত, জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর Help to the Study of Sanscrit ইত্যাদি বইগুলি প্রায় সর্বজনীন ভাবে পাঠ্য ছিল। কেন না, এগুলোর সাথে পাল্লা দেওয়া মতো গুণমানে উপযুক্ত আর কোনো বই ছিল না! বিদ্যাসাগরের কালেও ঘটনাটা এরকমই ছিল। এটা বোঝার জন্য এমনকি খুব বেশি তথ্যেরও প্রয়োজন হয় না। সামান্য সাধারণ বুদ্ধি থাকলেই হয়।
আর আরও আশ্চর্যের, যখন মার্ক্সবাদী বলে কথিত কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন তোলেন। বিদ্যাসাগর যে উনিশ শতকের উদীয়মান উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় মধ্যবিত্ত তথা (মার্ক্সীয় পরিভাষায়) বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন, এই সত্য মেনে নিলে তো বই লিখে এবং ছাপিয়ে ব্যবসা করায় তাঁদের আপত্তি করার কোনো মানে থাকে না। এরকমই তো করার এবং হওয়ার কথা! চুরি জোচ্চুরি ঘুসের কারবার তো তিনি করেননি! হ্যাঁ, পুস্তক ব্যবসায় সকলে সফল হয়নি বা হয় না, বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন স্কুল পাঠ্য বইয়ের বাণিজ্য থেকে।টাকা রোজগার করেছিলেন বলেই তিনি আবার সেই টাকা সমাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নানা রকম সংস্কার কর্ম এবং শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচির মাধ্যমে।
আনন্দবাজার পত্রিকা যখন কাউকে দিয়ে এই সব হাবিজাবি অভিযোগ তোলার জন্য প্রবন্ধ লেখায়, তাদের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বর্তমান কালের নেতামন্ত্রীদের খুল্লমখুল্লা চুরিদুর্নীতির হালুয়াভোজন দেখে যখন দেশের মানুষ বীতশ্রদ্ধ এবং বারবার পেছন দিকে তাকিয়ে অতীতের এই সব মহামানবদের চরিত্রের মধ্যে সান্ত্বনা এবং প্রেরণা খোঁজে, তখন এই সমস্ত বড় গণমাধ্যম চেষ্টা করছে সেই সুযোগটি কেড়ে নেবার, বড় বড় বিজ্ঞানী সাহিত্যিক দার্শনিক সমাজকর্মী কমিউনিস্ট ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে খুঁত বের করে কলঙ্ক ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সারা দুনিয়া জুড়েই বুর্জোয়া গণমাধ্যমে এই কাজ করে চলেছে। ওদের এই অপচেষ্টা থেকে শুধু মাত্র কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে মার্ক্স লেনিন মাও সে-তুং নন, এমনকি আইনস্টাইন সুভাষ বসু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর—কেউই ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। সকলকেই ওরা নামিয়ে আম পাব্লিক স্তরে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। সেই অনুযায়ী লেখক খুঁজে বের করে উপযুক্ত দক্ষিণা সহযোগে “নথীপত্র” ঘেঁটে উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সহ মনোগ্রাহী রচনা লিখিয়ে নিচ্ছে। সে দিক। কিন্তু সেই কাজে সমাজ সচেতন“বিপ্লবী” অনুসন্ধানী লেখকরা যুক্ত হবেন কেন?
তৃতীয় অভিযোগ, সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন না করে উলটে সেই সময় সংস্কৃত কলেজ ভবন ইংরেজ সেনাবাহিনীর জন্য ছেড়ে দেওয়া। এই অভিযোগটির দুটি অংশ। একটা হল সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করা না করার বিষয়; আর একটা হল, সংস্কৃত কলেজের বাড়ি ইংরেজ অনুগত সেনাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া।
প্রথম প্রসঙ্গে বলা ভালো, বিদ্যাসাগর যে সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ সমকালীন বুদ্ধিজীবীই করেননি। কেন করেননি, সে এক যথেষ্ট জটিল মুদ্দা। বাংলাসাহিত্যে এ নিয়ে কোনো আবেগ, গান, কবিতা, নাটক—কিছুই তৈরি হয়নি। এমনকি, যখন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে, সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় নিয়ে কাব্য নাটক লিখছেন, তখনও হয়নি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও কোনো কবিতা বা গান নেই সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। অতএব একেও সিধা মুৎসুদ্দি লাইনে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায় না! যায় না বলেই অমল ঘোষ বা বদরুদ্দীন উমরের লেখায় এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেও তাঁরা এটা নিয়ে কোনো রকম অভিযোগ তোলেননি। {সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন আমি এখানে মূলতুবি রাখছি।}
একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিদ্যাসাগর যখন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা দর্শন চিন্তার বিরুদ্ধে একটা শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছিলেন, তখন সেই সামন্তী রাজাদেরই পুরনো রাজ ফিরিয়ে আনার জন্য কোম্পানির ভারতীয় সেনাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান তাঁকে এবং তাঁর মতো সম মনোভাবাপন্ন মনস্বীদের সামাজিক অ্যাজেন্ডা হিসাবে খুব তেমন আকর্ষণ করেনি। বিদ্রোহের সূচনায় গরু শুয়রের চর্বি-গুজব অনুঘটক হিসাবে কাজ করায় এই উদাসীনতা আরও প্রকট হয়েছিল বলে মনে হয়।
এখন আমরা যদি বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তাহলে এই মনোভাব বা উদাসীনতা নিয়ে অভিযোগ করার কিছু নেই। তিনি শিক্ষক, ভাষা নির্মাতা, অনুবাদক, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, সমাজ সংস্কারক, বিদ্যালয় সংগঠক, পরিদর্শক, নারী শিক্ষার প্রচারক ও সংগঠক—এই যৎসামান্য(??) পরিচয়ে যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তিনি কেন রাজনীতি করলেন না, দল তৈরি করলেন না, নাটক লিখলেন না, নিদেন পক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাতে গরম গরম নিবন্ধ লিখলেন না—এই সব অবান্তর অবাস্তব দেশকাল-চেতনাবর্জিত প্রশ্নে ফেঁসে না যাই, তাহলে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা না হলে মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকবেই।
কিচ্ছু করার নেই। পছন্দ যার যার।
দ্বিতীয় মুদ্দা: সংস্কৃত কলেজের বাড়িটা কি বিদ্যাসাগর চাইলে না-ও দিতে পারতেন? সেই স্বাধীনতা বা অধিকার বা ক্ষমতা কি তাঁর ছিল? না, ছিল না। কলেজের তিনি শুধু অধ্যক্ষ। শিক্ষা ও অনুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ের আধা-মালিক। পুরোটা নন। তাঁর শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ প্রায় কিছুই বাকি আধা (এবং আসল) মালিকরা মেনে নেয়নি। কিন্তু কলেজের বাড়ির সম্পূর্ণ মালিক কোম্পানির সরকার। তথাপি সমকালীন সরকারি চিঠি চালাচালি থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর একটা ভাড়া বাড়িতে ক্লাশ চালানোর বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি নির্দেশ এসে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু দিন দেরি করেছিলেন। হিন্দু কলেজের বাড়ি আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল (ঘোষ দত্ত থেকে শুরু করে তাঁদের আজকের ভাবশিষ্য মুৎসুদ্দি গবেষকরা এক অত্যাশ্চর্য নিবিড় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে হিন্দু কলেজের ভারতীয় পরিচালকদের বিরুদ্ধে সেরকম কোনো প্রশ্নই তোলেন না; সেটা কি তাঁরা সব বড় বড় জমিদার বলে?) এবং সেখানে ক্লাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিতে শিক্ষা অধিকর্তা কড়া নির্দেশ দেন, খুব দ্রুত বাড়িটি ছেড়ে দেবার জন্য এবং ভাড়া বাড়িতে উঠে যাওয়ার জন্য।
তবে সরল রেখায় পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্লেষণের জন্য এত সব ঘটনার খবর না রাখলেও চলে, জানলেও তা ভুলে গেলেই হয়। কেন না, বিদ্যাসাগরকে নামাতে হবেই। সিঁড়ি না পেলে দড়ি বেয়েই! তাই দেখি, ঈশ্বরচন্দ্রকে নামাতে গিয়ে সরোজ দত্ত মশাই আবার নিজেই এতদূর নেমে গেলেন যে দাবি করে বসলেন, বিদ্যাসাগর নাকি স্বয়ং সংস্কৃত কলেজের বাড়িতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ছাউনি ফেলার জন্য “আহ্বান”জানিয়েছিলেন।
কোথায় পেলেন এই তথ্য?
জানার বা জানানোর দরকার নেই।
একজন “দালাল”-কে নিয়ে লিখছি, তার আবার অত তথ্য-ফথ্য কী?
মানে হল, তথ্য না পেলে বানিয়ে নাও। কজন আর কষ্ট করে ফাইল পত্তর ঘেঁটে আসল ব্যাপার খুঁজবে আর জানবে! তার উপর ১৯৬৯-৭০ কালে আবার বিপ্লবের যে তাড়া ছিল!!
[১০]
এই জাতীয় অভিযোগ আরও ছিল, এবং আছে। তার জন্য কত রকম যে দড়ি পাকানো হয়েছে ভাবা যায় না! “বাঙ্গালার ইতিহাস” (২য় ভাগ) রচনা নিয়ে; সংস্কৃত কলেজে শূদ্র ভর্তিতে আপত্তি নিয়ে; জনশিক্ষার “বিরোধিতা” নিয়ে; পরিশেষে “সহবাস সম্মতি বিল”’-এ আপত্তির ঘটনা নিয়ে।
আসুন, এক এক করে দেখি।
প্রথম কিস্সা, বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরামপুর খ্রিস্টীয় মিশনের অন্যতম পাদ্রি রেভঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখা Outline of the History of Bengal compiled for the use of youths of India বইয়ের ৫ম সংস্করণ (১৮৪৪)-এর অনুবাদ করে তিনটি খণ্ড লেখা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন। তাতে সিরাজউদ্দৌল্লার বাংলার সিংহাসনে আরোহন (১৭৫৬), পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ও পতন থেকে শুরু করে বেন্টিঙ্কের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের এক খণ্ড চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিনয় ঘোষ থেকে শুরু করে আধুনিক সমালোচকদের অভিযোগ হল, বিদ্যাসাগর এই বইতে দেশি শাসকদের খাটো করে দেখিয়েছেন, ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করেছেন, ইত্যাদি। অভিযোগের বহর দেখে মানতেই হয়, তাঁরা বেশ যত্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বইখানা পড়েছেন। অভিযোগ-অনুকুল বাক্যগুলি অন্তত মনোযোগ দিয়ে পড়ে বইতে দাগ দিয়ে রেখেছেন! যাতে উদ্ধৃতি দিয়ে সবাইকে দেখানো যায়।
আহা, নিশ্চয়ই খুব খাটালি গেছে তাঁদের।
তবে, সকলেই জানেন, চোখে চালসে হলে, চোখের মণির ধনাত্মক নজর বেড়ে গেলে এক সমস্যা হয়, কাছের জিনিস আর ভালো করে দেখা যায় না। এনাদেরও তাই হয়েছে। ফলে একই বইতে যে ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা ও নিন্দা করেও বেশ কিছু বাক্য আছে, এমনকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্বন্ধেও যে দু এক গণ্ডা মন্তব্য আছে, বেছে বেছে ঠিক সেই সব বাক্যই চালসের খাঁজে আটকে যায়। তখন বুঝতে পারি, ডাঃ অমল ঘোষ অত যত্ন করে তথ্য দিয়ে দিয়ে সবিস্তারে বিনয় ঘোষ সরোজ দত্তদের প্রতিটি মন্তব্যের ভুলগুলি ধরিয়ে দেবার চল্লিশ বছর পরও কেন তাঁদের উত্তরাধিকারীরা আজও সেই একই ছকে আটকে আছেন। আসলে তাঁরা সকলেই চোখও দেখাননি, ধনাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন চশমাও নেননি। ফলে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একই রকম ভুলগুচ্ছ থেকে যাচ্ছে।
সত্যি কথা বলতে কী, তাঁদের এই সমস্যা হয়েছে তথ্যপাঠ থেকে নয়, পঠিত তথ্যকে সঠিক প্রেক্ষিতে বোঝার ক্ষেত্রে। আবারও আমাকে কার্ল মার্ক্সের ১৮৬৫ সালের সেই সাবধান বাণীটি স্মরণ করতেই হচ্ছে—সত্যকে উপরে উপরে (অর্থাৎ, শুধু মাত্র তথ্য সমষ্টি হিসাবে) দেখে ধরা যাবে না; তথ্যসমগ্রের খোলসের ভেতরে ঢুকে উঁকি দিতে হবে, যুক্তির মশাল জ্বালিয়ে দেখতে হবে, তবে যদি কিছু দেখা যায়।
বিদ্যাসাগরের তখন বাংলায় নানা ধরনের বই দরকার। ভাষা চর্চার পাশাপাশি বাংলায় ইতিহাস পাঠেরও অভ্যাস তৈরি করা দরকার। হাতের কাছে অন্য কোনো বই নেই। মার্শম্যানের বই তখন অন্যেরাও অনুবাদ করছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন ১ম খণ্ড এবং ভূদের মুখোপাধ্যায় ৩য় খণ্ড অনুবাদ করেছিলেন। {সেই সব বই নিয়ে অবশ্য সমালোচকদের কোনো মাথাব্যথা নেই!} তিনিও তাই এক (২য়) খণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন। তখন যদি তিনি ইংরেজ কুঠিয়াল বা সেনাপতিদের সমালোচনা করে নিজে একখানা ইতিহাস বই লিখতেন, সেই বই সরকারি বদান্যতায় গড়ে ওঠা স্কুলে যে পড়ানো যেত না, এটা ঈশ্বরচন্দ্র বুঝলেও ঘোষ দত্ত বা তাঁদের শিষ্যদের মাথায় ঢোকেনি। এমনকি, শুধু ঔপনিবেশিক সরকার নয়, উত্তর-উপনিবেশ সরকারের আমলেও যে বিরোধী বা বিকল্প মতামতের দুচার ফোঁটাও পাঠ্যবইতে স্থান জোটে না, এটা দেখার পরেও। জওহরলাল নেহরুর আমলে রমেশ চন্দ্র মজুমদার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস স্বাধীনভাবে লিখবার অনুমতি পাননি। কংগ্রেসি ফরমান অনুযায়ী লিখতে বলা হয়েছিল। গান্ধী নেহরু প্যাটেল পন্থকে একটু বাড়তি আলো দিয়ে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের, কমিউনিস্টদের, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভূমিকা যতটা পারা যায় খাটো করে। দেশ বিভাজনের সম্পূর্ণ দায়ভার কায়দা করে জিন্না এবং মুসলিম লিগের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে। প্রতিবাদে তিনি সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এসে ভারতীয় বিদ্যাভবনের পৃষ্ঠপোষকতায় তের খণ্ডে ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস গ্রন্থাবলির সম্পাদনা করেন এবং নিজেও প্রতিট খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায় লেখেন। ফলে, উনিশ শতকের মধ্য পর্বে সেদিন কী হত জানা ছিল বলেই হয়ত বিদ্যাসাগর কোনো রকম ঝুঁকি নেননি।
তা সত্ত্বেও তিনি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সুকৌশলে দুচার কথা সমালোচনার ছলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, বিচারক ইম্পি—প্রত্যেকের সম্পর্কেই কিছু না কিছু নিন্দা সূচক মন্তব্য প্রয়োগ করেছেন। সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ হয়ে লিখলে যে এমন সব উক্তি করা যায় না, একেবারে সাদা চোখে পড়েই বোঝা সম্ভব। তবু যে অনেকেই তা দেখেননি বা বোঝেননি, তার কারণ হল, তাঁরা সিদ্ধান্তগুলো অনেক আগেই করে ফেলেছেন: “রেনেশাঁস হয়নি”,“রামমোহন রায় দালাল”, “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজভৃত্য”—ইত্যাদি। এতটা কড়া ছানি-পড়া চোখ নিয়ে তথ্যের সাগরে সাঁতার কাটা হয়ত যায়, ডুবুরির দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে ওঠে।
না হলে, কতটা ছানি পড়লে তবে ১৮৪৮ সালে লেখা ও প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস” সম্পর্কে গাল পাড়তে বসে সরোজ দত্ত (শশাঙ্ক ছদ্মনামে) লিখতে পারেন, যখন ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হচ্ছে (১৮৫৭), তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বসে বিধবা বিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬) করে সেদিক থেকে লোকের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বাংলার ইতিহাস রচনার (১৮৪৮) মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকদের প্রশস্তি গাথা লিখছিলেন! সাল তারিখগুলো তিনি জানতেন না—এ তো আর হতে পারে না। এত বড় অভিযোগপৃক্ত বয়ান তিনি না জেনে লিখবেনই বা কেন? আর যখন লিখেই ফেললেন, শিষ্যরা অন্তত এই মারাত্মক ভুলগুলো ধরে ফেলতে পারত।
কোনোটাই হল না। তাঁরাও মিথ্যাচারিতার সেই পতাকাকে উঁচুতেই তুলে রেখেছেন। এই সব দেখে আমার মনে আজকাল কেন জানি না আধা সন্দেহ হচ্ছে—বিজেপি কি তাহলে সরোজ দত্তদের কাছেই ইতিহাসের তথ্য ও সালতারিখ জালিয়াতির প্রথম পাঠ শিখেছিল? কে জানে!
সে না হয় হল। এবার পরের প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।
বিদ্যাসাগর কি সংস্কৃত কলেজে কায়স্থের বাইরে অন্যান্য “নিম্ন” বর্ণের ছাত্রদের প্রবেশ আটকে দেননি? ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত“জনশিক্ষা”-র কর্মসূচির বিরোধিতা করেননি?
আবার বলতেই হচ্ছে, আপাত দৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হয় বৈকি! কিন্তু গভীরে নজর ফেলতে পারলে অন্য সত্য ধরা পড়তেও পারত। বিনয় ঘোষদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ত সেটা।
প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্ম প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথার দীর্ঘপ্রচলিত নিগড় একবার ভেঙে দিতে পারলে, কায়স্থদের দিয়ে যার শুভ সূচনা, অনতিবিলম্বেই যে সেই বর্ণ নির্বিশেষে, এবং অবশেষে ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে শিক্ষার দরজা খুলে দেবার দাবি সমাজের বুকে উঠতে শুরু করবে, এটা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে বলে বিদ্যাসাগর ভাবেননি। বাংলায় তখন কায়স্থদের মধ্যে বেশ খানিকটা জাগৃতি এসেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষাকে প্রসারিত করে দিতে পারলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা হবে। যে দেশে রাণি রাসমণি জাতে কৈবর্ত (শুদ্র) বলে (স্কুল নয়) মন্দির স্থাপন করার জন্যও হিন্দুদের কাছে জমি পাচ্ছিলেন না, এবং মন্দির নির্মাণের পর কোনো ব্রাহ্মণ পূজারী সেখানে পূজাপাঠের দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছিল না, সেখানে বিদ্যাসাগর যদি শূদ্রদের জন্যও সংস্কৃত কলেজের দরজা তখনই খুলে দিতেন, তা কার্যকর তো হতই না, এমনকি যে কায়স্থদের কথা তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভেবেছিলেন, তাদেরও কলেজে প্রবেশাধিকার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠত সেকালের গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু মাতব্বরদের হুল্লোড়বাজির ঠেলায়।
আমরা “ঈশ্বর”কে ধন্যবাদ দিই তিনি সরোজ দত্তর মতো বিপ্লবীপনা দেখাতে যাননি বলে। তিনি তাঁর দেশ সমাজকে চিনতেন। জানতেন, কীভাবে সাবধানে পা ফেলতে হবে। এক পা এক পা করে এগোতে হবে। প্রথমে ধীরগতির পরিমাণগত পরিবর্তন। তারই পরিণামে একদিন আসবে ঈপ্সিত গুণগত পরিবর্তন। সেদিন তিনি গাঁইতি শাবল হাতুড়ি আর আলকাতরা দিয়ে আধা-সামন্ততন্ত্রকে ভাঙার পথনাটিকায় অভিনয় করতে যাননি, পুরোটাকে ভাঙার কাজটাই শুরু করেছিলেন বাস্তবে। হাতেকলমে। নাগপুর বা নরেন্দ্রপুরে খবর নিলেই সেই কারণে সামন্ততন্ত্রের তরফে বিদ্যাসাগরের প্রতি সরকারি মনোভাবটা জেনে নেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর যেমন সামন্ততন্ত্রকে চিনতেন, ওনারাও তেমনই বিদ্যাসাগরকে চেনেন!
তিন নং মামলা: জনশিক্ষা।
বিনয়বাবুদের কল্পনাশক্তির বলিহারি যাই যে তাঁরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করতে এসে এই উপনিবেশে নাকি জনশিক্ষার যথার্থ বিস্তার ঘটাতে চাইছিল, আর তাতেই বিদ্যাসাগর বাগড়া দিয়ে বসলেন! আর তাঁদের দেখাদেখি স্তরে স্তরে তাঁদের ভাবশিষ্যরাও এই বিশ্বাসটিকে বিনা বিচারে বহন করে চলেছেন। এই প্রশ্নটাতে এমনকি বদরুদ্দীন উমর সাহেবও বিভ্রান্ত হয়ে সায় দিয়ে ফেলেছেন।
অথচ বিদ্যাসাগর কিন্তু সেদিন সাহেবদের চালাকিটা শুরুতেই ধরে ফেলেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে যেটুকু টাকাপয়সা এতদিন সরকার বাহাদুর ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির জন্য খরচ করছিল, সেখান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে জনশিক্ষা বিস্তারের নামে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলবে। তাতে না হবে জনশিক্ষা, না যাবে বর্তমান সীমিত সংখ্যক স্কুলগুলোকে চালানো। জনশিক্ষার কাজ হবে না, কেন না, দেশের বেশির ভাগ গরিব পরিবার যাদের ভালো করে দুবেলা খাওয়াই জোটে না, তাদের কাছে সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করতে স্কুলে পাঠানো এক ভাব বিলাসিতা বই অন্য কিছু নয়। স্কুলের বেতনও তারা দিতে পারবে না, পাঠ্যবই কেনার খরচও তারা সামলাতে পারবে না। অথচ, চালু স্কুলগুলোর বরাদ্দ কমে গেলে তার ব্যয়ভার কে বহন করবে? তাই তিনি সরাসরি বিরোধিতা করে বসলেন সেই প্রস্তাবকে।
কিন্তু বিনিময়ে তিনি আর কী বললেন?
হ্যাঁ, সেইটা আবার বিনয়বাবুরা জানাতে ভুলে যান তাঁদের পাঠকদের। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তোমরা যদি যথার্থই জনশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চাও, তাহলে শিক্ষাকে করতে হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তবেই তারা হয়ত ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হবে। তা কি তোমরা করতে রাজি আছ? যদি রাজি থাক, তবে আমি এই প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানাব।
বিপ্লবী হওয়া আর বিপ্লবী সাজার মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য থাকে বইকি! ডাঃ অমল ঘোষ {দেবব্রত চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্য অনুসারে যতটা বুঝেছি}বিপ্লবী হতে চেয়েছিলেন, সাজতে নয়। বিলাসপুরের গরিব মানুষদের মধ্যে নিজের হাতে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার জন্য আত্যন্তিক সদিচ্ছার পাশাপাশি কতখানি বাস্তব দূরদর্শিতার দরকার হয় তা আত্মঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি এই রকম প্রতিটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের সদর্থক ভূমিকাকে, পরিমিত পদচারণাকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলমের সমস্ত কালিশক্তি দিয়ে তাঁকে সমর্থনও করে গেছেন! বাকিদের ছিল (হয়ত তাঁদের অগোচরেই) কয়েক দিনের (বা রাতের) জন্য বিপ্লবের শ্রুতিনাটক। উষ্ণ বিনোদন! তাই তাঁদের কথার সমাকলনে কোনো সীমা পরিসীমার বালাই ছিল না। বা অনুরূপ ভূমিকার্থীদের আজও নেই!
তাঁদের তাই ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়নি বা হয় না!
ষষ্ঠ (শেষ) পর্ব এই লিঙ্কে
লেখক পরিচিতি: ‘সেস্টাস’ নামে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের আলোয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে লোকপ্রিয় প্রবন্ধের লেখক।


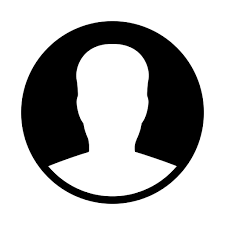
অনুরোধ করছি ভাইবোনবন্ধুজন সবাই একবার পড়ুন।